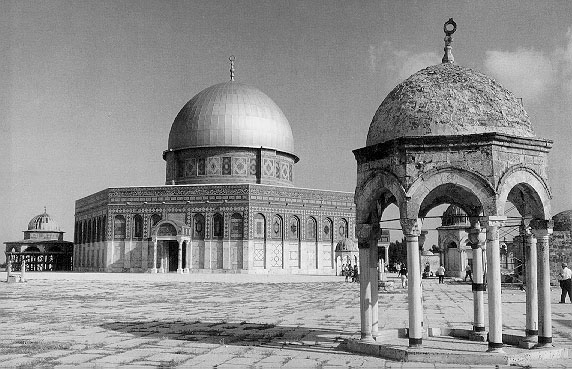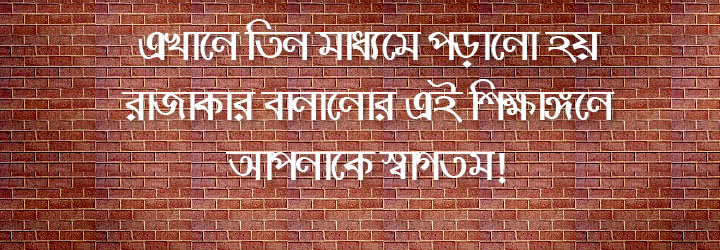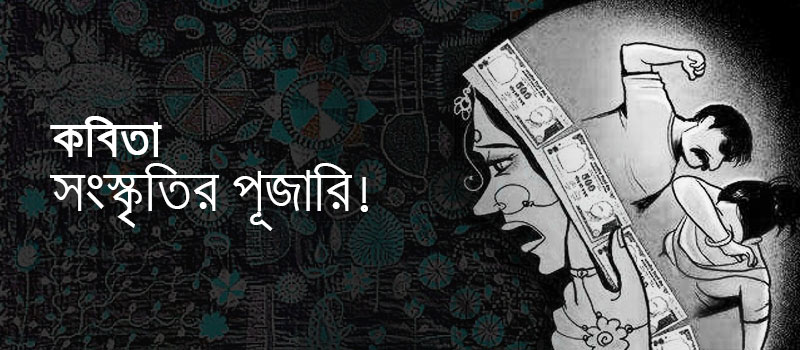ছেঁড়া টিকেটের দূর্নীতি, দারিদ্র ও অকৃতজ্ঞ বাঙালি
প্রথমেই আমার আপত্তি ঐ “দূর্নীতি” শব্দটাতে। শব্দটার বহুল ব্যবহার, এই নেতিবাচক শব্দটিকে শ্রেফ আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না। এক্ষেত্রে আমরা একটু euphemism বা সুভাষণ কাজে লাগিয়ে শব্দটাকে যদি বদলে লিখি “নীতিভ্রষ্টতা”, তাহলে সেটা জোরালোভাবে মাথায় গিয়ে টোকা দেয় না, অথচ মূল কথা ঠিকই বলে। তাই এই নিবন্ধের শিরোনাম হওয়া উচিত “ছেঁড়া…