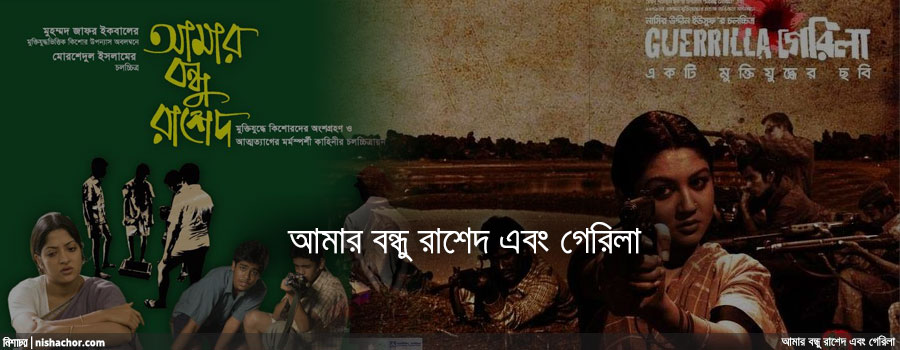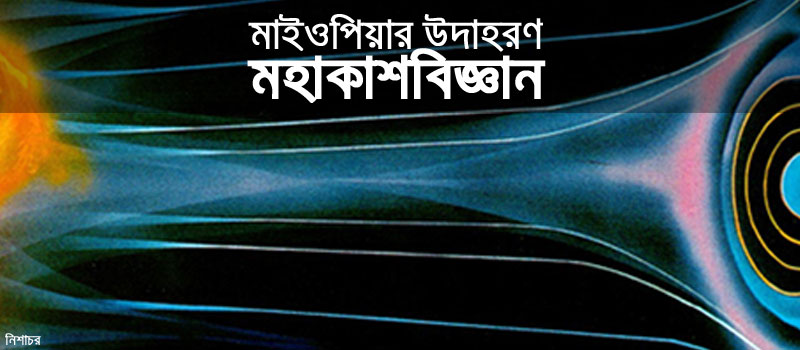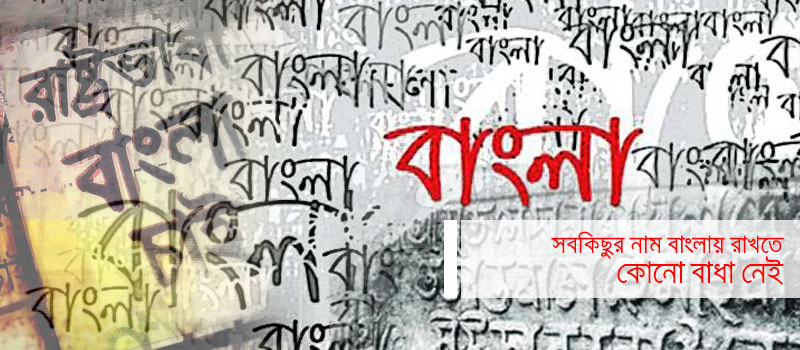অপচয়!
হুহুঁ, সময়ের অপচয় করো না। —এরকম আপ্ত বাক্য নিয়েই সব সময় চলচ্চিত্র দেখতে বসতে হয় নাকি আমাদের? নাকি কেউ চলচ্চিত্র দেখতে বসেছে বলে আমরা মনে করি, সে জীবনে একটা মহা কিছু অর্জন করতে যাচ্ছে?
দুটোর মধ্যেই দুটোই খুব এক্সট্রিম, মানে চরম ভাবনা। এতো কাটাকাটাভাবে বিনোদনকে ভাবতে নেই। বিনোদনকে নিছক বিনোদন হিসেবেই দেখতে শেখা উচিত –অন্তত আমাদের গুরুজনরা এমনটাই আমাদের শিখিয়েছেন।
কিন্তু তারাই আসলে কথা রাখেননি। যখন প্রোপাগান্ডা চলচ্চিত্র তৈরি হয়, তখন বিনোদন আর বিনোদন থাকে না, তখন সেটা একটা এক্সট্রিম ম্যাসেজ নিয়ে আসে দর্শক-শ্রোতার কাছে: দর্শক-শ্রোতাকে বলে তোমাকে কিছু অর্জন করেই চলচ্চিত্রটা শেষ করতে হবে। সেখানে সময়ের অপচয় বলে কোনো কথা নেই।
আর সেজন্য প্রোপাগান্ডা চলচ্চিত্রকে হতে হয় যথেষ্ট সুনির্মিত, কাঠামোবদ্ধ; কাহিনী হতে হয় আকর্ষণীয়। সেখানে থাকতে হয় শব্দ আর ছবির অপূর্ব সম্মিলন, যেন দর্শক খামখেয়ালিভাবে দেখতে দেখতে একসময় ডুবে যায় কাহিনীর ভিতরে, এবং ছবি দেখা শেষে তারা আবিষ্কার করে, তারা ছবির কোনো না কোনো একটা ভালো লাগা চরিত্র। তখনই প্রোপাগান্ডা ছবি সার্থক হয়।
দেখা শুরু করলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র “আমার বন্ধু রাশেদ”। কয়েকটা কারণে ছবির প্রতি আমার এক্সপেকটেশান একটু বেশি। কারণ ১: কাহিনীটা মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের। কারণ ২: ছবির পরিচালনায় ছিলেন “দিপু নাম্বার টু”–খ্যাত পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম। কারণ ৩: আমার ফুফাতো ভাই শাকির বলেছে, ছবিটা সুন্দর!
ছবির শুরুতে একটা ট্রেন আসছে। ক্যামেরা সেই ট্রেনটাতে উঠে গেলো এবং শেষ বগির দরজা দিয়ে বেরিয়ে রেললাইনটা ধরলো। অপূর্ব দৃশ্য! কিন্তু কানে কেমন জানি বেখাপ্পা লাগছিল ট্রেনের শব্দটা। আমরা জানি ট্রেনের শব্দ কিছুটা একঘেয়ে, ঝক্কর ঝক্কর, কিন্তু আসলে তা কিন্তু না, সেখানেও আছে একটা ছন্দ এবং ছন্দপাতের খেলা, সেকারণেই একেবারে একঘেয়ে লাগে না। কিন্তু আলোচ্য দৃশ্যে ট্রেনের শব্দটা ছিল ছোট্ট, কেবল একটা মাত্র ট্র্যাক (track), আর তা রিপিট করা হচ্ছিল বলে শব্দটা মেকি, ধরা যাচ্ছিল। কিন্তু যখন ট্রেনের ভিতরে দুটো চরিত্র কথা বলা শুরু করলো, তখন সেই কাঙ্ক্ষিত ছন্দপাতটা কাজ করলো বলে ফাঁকটা আর ধরা পড়লো না।
কিন্তু এ কী? খটকা লাগলো, যখন ছবির প্রথম ডায়লগটা কানে এলো, “আচ্ছা বাবা? এখন যদি তোমার কোনো বন্ধুর সাথে দে-খা হয়ে যায়? তুমি কি বলবে? কীরে দোস্ত, কেমন আছিস। বলবে বাবাহ্?” –এই বাক্যের ভুল বিরামচিহ্ন দেখে যেমন থমকে যাবেন, ঠিক এমনটাই থমকে গেছিলাম আমি ঐ বালকের অভিনয় দেখে, এ যেন বইয়ের পাতা থেকে কোনো স্কুলবালক সুরে সুরে মুখস্ত পড়া আওড়াচ্ছে!
প্রত্যেকটা কিশোর-চরিত্রের চোখে পড়ার মতো কিছু মুদ্রাদোষ ছিল: তারা যখন সোজা হয়ে কোথাও দাঁড়ায়, তো তাদের দুই হাত শরীর ঘেষে দুপাশে এমনভাবে গায়ের সাথে সেঁটে থাকে, মনে হয় কেউ তাদেরকে এ্যাটেনশান করে রেখেছে; তারা যখন শুয়ে থাকে, তখন সটান হয়ে আকাশের দিকে মাথা দিয়ে শোয়, আর একটা হাত থাকে পেটের উপর; তারা বিছানা থেকে যখন উঠে, তখন বোঝাই যায়, তারা আরামের জন্য বিছানায় ঘুমায়নি, সোজা-সটান উঠে বসে, অথচ তাড়া না থাকলে আমরা কেউই ঘুম থেকে সোজা-সটান উঠে বসি না, কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে শরীরটাকে তুলতে চেষ্টা করি।
কিশোর চরিত্রগুলো যেখানে মুখ্য ছিল, তাদের অভিনয়শৈলী হওয়ার দরকার ছিল দৃষ্টিনন্দন, আকর্ষণীয়। কিন্তু কোথায় কী? ক্যামেরা যখন “রোল” বলে, তার এক সেকেন্ড পরে তাদের মুভমেন্ট শুরু হয়। দেয়াল থেকে দুই বালক একসাথে নামবে —এমনই নির্দেশ ছিল। তো একজন নামতে উদ্যত হয়ে আরেকজনের মধ্যে নামার লক্ষণ না দেখে থমকে দাঁড়ায়, তারপর দুজন একসঙ্গে নামে— কোনো সমস্যাই হয়তো নয়, কিন্তু বড্ড দৃষ্টিকটু। কিশোর অভিনেতাদের চোখের, ভ্রু’র এক্সপ্রেশনের বালাই নেই। …এতটুকু বাচ্চা অভিনেতাদের প্রতি আমার হয়তো এতোটা কঠোর হওয়া উচিত হচ্ছে না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, নায়ক রাশেদ চরিত্রের (চৌধুরী জাওয়াতা আফনান) অভিনয়টা যেখানে ফুটে উঠছিল, সেখানে বাকি চরিত্রগুলো বড় বেশি ম্লান লাগছিল। কিন্তু মুদ্রাদোষগুলো ছিল প্রতিটি কিশোর চরিত্রেই।
বয়স্ক অভিনেতাদের কাছে একটু বেশি আশা করা দোষের কিছুই নয়। কিন্তু দিপু নাম্বার টু-তে যেখানে আবুল খায়ের-এর (তাঁর বিদেহী আত্মার ক্ষমা কামনা করি) মায়াময়ী শিক্ষকের ভূমিকাটা বড় দাগ কেটেছিল, সেখানে ইনামুল হকের অভিনয়টা শ্রেফ ভাড়ামি মনে হচ্ছিল। [ইবুর বাবা চরিত্রে] পিযুষ বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয়, পিযুষের মতো উচ্চতা ছুঁতে পারছিল না। তাছাড়া দেশের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে পিযুষকে যখন ক্লিন শেভ্ড দেখা যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, এতোদিনের অভিনয় জীবন কস্ট্যুম সম্বন্ধে আমাদের অভিনেতাদের কিছু দেয়নি বোধহয়।
প্রায় পুরোটা ছবি জুড়ে অভিনয় দেখেছি আমি হুমায়রা হিমুর চরিত্রে (অরু আপা)। যদিও প্রথম দিককার ডায়লগগুলো তার ক্ষেত্রেও মেকি লাগছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মেয়েটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তারপরও, প্রেমিকের গুলি খাবার খবরে আহত হয়ে হিমুকে যখন নিজের টালমাটাল শরীরটাকে ধরে রাখার জন্য বেশ কয়েক পা পিছাতে পিছাতে পিছাতে পিছাতে গিয়ে টেবিলে ঠেস দিতে হলো, তখন পরিচালকের অদূরদর্শিতা বড় বেশি স্পষ্ট লাগছিল।
ভালো অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের জোলি— ওয়াহিদা মল্লিক জোলি (ইবুর মা)। অভিনয় খুব ভালো লেগেছে ডাক্তার চরিত্রে খলিলুর রহমান কাদেরীর। [বড় ইবুর চরিত্রে] রাইসুল ইসলাম আসাদ খারাপ করেননি, কিন্তু তাঁর ঐ আলগা চুলটা বড় বেশি চোখে লাগছিল। অভিনয় খুব খারাপ করেননি মুরাদ পারভেজও। আবার স্বভাবসুলভ ভালো অভিনয় দিয়ে মন জয় করেছেন [রাজাকার চরিত্রে] গাজী রাকায়েত।
বাস্তবের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ বড় বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে এমন কিছু মুহূর্ত তৈরি করতে হয়, যখন মানুষ সংকটাপন্ন। আর সেই আবহ এনে দেবার জন্য দরকার একটা ধীরস্থির প্লট, যেখানে ক্যামেরা চলবে ধীরে, কাহিনী চলবে ধীরে, প্রত্যেকটা চরিত্র যার যার জায়গায় বড় বেশি একা, ছন্নছাড়া। কিন্তু এই ছবির কাহিনীতে ঘটনার পর ঘটনা আসতেই থাকে। যখন দর্শক কোনো দুঃখের দৃশ্যে চোখ নিবদ্ধ করতে যায়, তখনই দৃশ্যপট পাল্টে গিয়ে গতিশীল দৃশ্য এসে মনকে চঞ্চল করে তোলে।
চরিত্রগুলো চিত্রণ যতটা অসুন্দর হবে বলে মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি অসুন্দর চরিত্রগুলোর অভিনেতা-অভিনত্রীরা। নতুনদের দিয়ে কাজ করিয়ে তারেক মাসুদ অভিনেতা তৈরি করেননি, বরং তৈরি অভিনেতা তুলে এনেছিলেন। আর এখানে মনে হয়েছে, ছবিটা আসলে অভিনেতা তৈরি করার একটা মাধ্যম। হিন্দু বন্ধুটি যেখানে বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল, সেখানে হঠাৎ করেই পিছনে হাজির হলেন মুসলমান বেশভুষায় হিন্দু মা, আর বোন। মায়ের কপালের সিঁদুরটা মুছে ফেলাসত্ত্বেয় দেখা যাচ্ছিল তার রেশ —না এখানে ভুল ছিল না, ছিল দর্শককে বিষয়টা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা। কিন্তু ছেলে যেখানে ভ্যা ভ্যা করে কাদছিল, মা আর বোন সেখানে শ্রেফ ভাবলেশহীন রোবট। অপূর্ব কৃষ্টিসম্পন্ন অতীতকে পেছনে ঠেলে মুসলমান বেশ ধরতে তাদের যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছিল না।
যখন মিলিটারি প্রথম এসে নামে শহরে, তখন রাজাকার হবার আহ্লাদে এগিয়ে আসেন জনৈক মৌলভি। কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস না করে হানাদাররা গুলি চালায়। কিন্তু বন্দুকটা যখন দক্ষিণ দিকে মুখ করা, তখন পূর্ব দিকে দৌঁড়াতে থাকা রাজাকারের চ্যালা কিভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, সেই প্রশ্ন আমি রাখছি পরিচালকের কাছে।
জাফর ইকবাল স্যারের লেখা পড়তে পড়তেই বড় হয়েছি। কিন্তু এখন সেই ধারও বোধহয় কমতে শুরু করেছে। কোথায় যেন বড্ড বেশি রাজনীতি জায়গা করে নিয়েছে সেখানে। “আমি অনিক” বইটির গাজাখুরি গল্পেও যেখানে ছেলেটার সেরা গণিতবিদ হবার বর্ণনা পড়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আমার বন্ধু রাশেদ-এর মতো ভালো গল্পের বর্ণনা তিনি বড্ড দায়সারাভাবে দিয়ে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ রেখে দিয়েছেন। …একজন কিশোরকে দিয়ে অস্ত্রের কাহিনী বলানোটা অবাঞ্চিত ছিল না, কিন্তু ছিল সেই অস্ত্রটা কিভাবে চালাতে হয়, তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়াটা। কিভাবে পিন খুলে হাত ঘুরিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়, তা দেখিয়ে কিশোর মনকে মুক্তিযুদ্ধ-সচেতন আর পাকিস্তানবিদ্বেষী করা হয় না, বরং কিভাবে গ্রেনেড ছুঁড়ে কৈশোরেই বোমাবাজ হওয়া যায় –তাও শিখানো হয় – শিশু মনোস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম বিষয়টি কি জাফর ইকবাল স্যারের মতো বিজ্ঞানী এড়িয়ে যাননি?
পরদিনই দেখতে বসলাম আংশিক সরকারি অর্থায়নে তৈরি দ্বিতীয় চলচ্চিত্র “গেরিলা”। উইকিপিডিয়ায় পানাম নগর নিবন্ধটার পরিবর্ধন করতে গিয়ে প্রথম জানতে পারি গেরিলা চলচ্চিত্রের শ্যুটিং হচ্ছে ওখানে। তারপর অপেক্ষা করে ছিলাম ওটা দেখার জন্য।
যখন দেখা শুরু করলাম, স্বভাবতই আমার ক্রিটিক মন সন্দেহবাতিকগ্রস্থভাবে খুঁটতে থাকলো ভিতরে। এবং শুরুতেই দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না, ২৫ মার্চ রাতের প্রতিরোধ গড়ে তোলায় ব্যস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বন্দুকের নল থেকে পটকার বারুদ পুরপুর করে বেরোচ্ছিল, বোঝাই যাচ্ছিল, ওখানে মেশিনগানের গুলিটা ভাওতা। আবার নজরে এলো ভাষার গানের রচয়িতা আলতাফ হোসেনের স্ত্রীর চরিত্রের অভিনেত্রী নিজের বাম হাতটাকে হাস্যকরভাবে পেটের কাছে বাঁকা করে ধরে রাখেন। শ্রুতিকটু লাগছিল প্রধান চরিত্রের ভাষার রদবদলগুলো- কখনও ঢাকায় প্রচলিত মিশ্র ভাষায় বাকচারিতা, কখনও গ্রাম্যটানে কথা বলা, কখনও খাঁটি শুদ্ধ বাংলার ব্যবহার; অথচ সর্বত্র এই ভাষার বদলগুলো দৃশ্যের প্রয়োজনে হয়েছে বলে মনে হয়নি। বিলকিসের মা/বাবা যখন মারা যান, তখন ভাই খোকনের ডায়লগও বড্ড মেকি লাগছিল। মামা আলেফ মোক্তার যেখানে খাঁটি গ্রাম্য ভাষায় শিশু বিলকিস আর তার ভাই খোকনের সাথে গল্প করছিলেন, পরের দৃশ্যেই ছোট্ট ঐ দুই গ্রাম্য শিশুর মুখে, “খোকন, সাবধানে, পাখিটা যাতে ব্যথা না পায়” —এরকম খাঁটি শুদ্ধ ভাষাও বড্ড মেকি লাগছিল।
কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ঘটনার বুনন, নির্মাণশৈলী, কাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিক পরিবর্তনগুলো আমার সন্দেহবাতিক মনকে কখন যে টেনে নিয়ে যায় গভীরে, বুঝতে পারিনি। জয়া আহসান সব সময়েরই ভালো অভিনেত্রী। সব ধরণের চরিত্র করতে তাঁর জুড়ি নেই। আবারও তিনি প্রমাণ করেছেন, তাঁর অভিনয়ের প্রতিভা। খুব টেনেছে, যখন একমাত্র ভাই খোকনকে হারানোর পরে মাটিতে পড়ে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেসে যায় বিলকিস —বুঁদ হয়ে দেখছিলাম। …অভিনয়ে আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসা এটিএম শামসুজ্জামান তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয় দিয়ে বরাবরের মতোই মাত করেছেন এখানেও। অপূর্ব অভিনয় দিয়ে পুরোটা ছবি ধরে রেখেছেন পাকিস্তানী মেজর সারফারাজ ও ক্যাপ্টেন শামসাদ খান —দুটো চরিত্রে অভিনয় করা শতাব্দি ওয়াদুদ। আলতাফ মাহমুদকে সঠিকভাবে চিত্রায়ন করতে পেরেছেন কিনা আহমেদ রুবেল, সে তাঁরাই ধরতে পারবেন, যাঁরা তাঁকে বাস্তবে দেখেছেন; তবে আমি বলবো, রুবেল তাঁর চরিত্রের অবমুল্যায়ন করেননি। হিন্দু দুধওয়ালার অভিনয়, অল্পবয়স্ক নারীলিপ্সু রাজাকার যুবকের তীব্র লিপ্সা, বিলকিসের কাজের মেয়ের উর্দু-বাংলায় বাকচারিতা —এরকম ছোট ছোট চরিত্রগুলোও মুগ্ধ করে যাচ্ছিল আমাকে। —সোজা কথা, চরিত্রগুলোর অভিনয়, যার যার অবস্থান থেকে মুগ্ধ করেই যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে, আমাকে গ্রাস করে নিয়েছিল কাহিনীর গভীরে।
সব শেষে যখন লোবান জ্বালানো ধূপ দিয়ে কালীপূঁজার মতো করে মুসলমান বিলকিস গ্রেনেডের ধূপে সাঙ্গ করে দিলো ক্যাপ্টেন শামসাদের আস্তানা, তার মাঝেই ফুটে উঠেছিল বীরাঙ্গনাদের ত্যাগ আর সব খোয়ানো বাঙালির দেশ-অর্জনের মহৎ প্রাপ্তিটুকু। আমার শ্রদ্ধা উপচে পড়ে সৈয়দ শামসুল হকের প্রতি, কারণ তাঁর “নিষিদ্ধ লোবান”ই এই চলচ্চিত্রের মূল কাহিনী করা হয়েছে।
আংশিক সরকারি অনুদানসত্ত্বেয় গেরিলার তীব্র আকর্ষণ আর পূর্ণ অনুদানে নির্মিত আমার বন্ধু রাশেদের চুম্বকীয় বিপরীত প্রতিক্রিয়াই আমাকে একপক্ষ নিতে বাধ্য করেছে। তখনই বোধকরি আলাদা করতে পেরেছি, কোনটা অপচয়, আর কোনটা চয়ন। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না, গেরিলা’র নির্মাণে ভারতের বিভিন্ন প্রযুক্তির সহায়তা নেয়া হয়েছে ফলাও করে, আমার বন্ধু রাশেদ-এর প্রসেসিং আর প্রিন্টিং হয়েছে ভারতে। তবে একথাও মনে হয়েছে, মোরশেদুল ইসলাম বোধহয় তাঁর সমালোচকদের না শুনলেই ভালো করতেন, কারণ তিনি নাকি ধীরগতির ছবি বানান বলে অনেকেই সমালোচনা করায় তাঁর এই ছবিটাতে গতি এনেছেন। …অপচয় করেছেন। অপচয়।
-মঈনুল ইসলাম