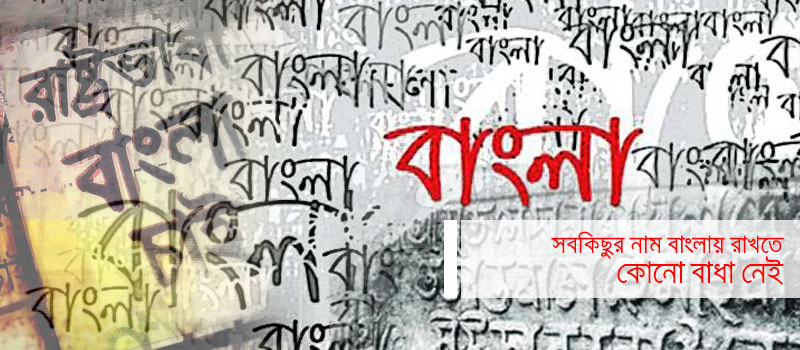ছোটবেলা থেকে শুনে আসছিলাম ঘটনাটা – ভাসা ভাসা। মামার কাছে তাই আগ্রহভরে বলেছিলাম, আমাকে সময় করে সেই ঘটনাটা বলতে। যতটুকু আগ্রহ নিয়ে বলেছিলাম, তার চেয়ে তিনগুণ বেশি আগ্রহ দেখিয়ে তিনি ৪ দিনের মাথায় আমাকে খবর পাঠালেন, তৈরি। কী? মামা আমাকে বলার জন্য অপেক্ষা করেননি, নিজেই লিখে ফেলেছেন। তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপিটা আমার হাতে দেবার আগে আমাকে পড়ে পড়ে শোনালেন। তাঁর চোখে মুখে সে কী দৃষ্টি, যেন এখনই সামনে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মানুষ। …হ্যা, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধা নন; অস্ত্র হাতে হলেই বোধহয় ভালো ছিল! তাহলে আর ‘সিভিলিয়ান’ হিসেবে গণ্য হতেন না। হাসতে হাসতে জীবনটা দিতেন। কিন্তু শুধু খোদার দেয়া প্রাণটা নিয়ে তিনি (বা তাঁরা) কীইবা করতে পারতেন, জীবন রক্ষা ছাড়া। হ্যা, একজন সিভিলিয়ানের মুখে শুনুন সেই রক্তাক্ত দিনগুলোর কথা। তাঁর সেই পাণ্ডুলিপিটাতে আমি কলম ছোঁয়াতে ভয় পেয়েছিলাম। কী গোছানো লেখা, কী বাস্তব সেই পরিস্থিতি, কী সিদ্ধহস্ত তাঁর সাহিত্যিক লেখনী! কিন্তু শুধু পাঠক গ্রহণযোগ্যতা বিচারে আমাকে ভাষাগত যৎসামান্য রদবদল করতে হয়েছে। নয়তো পুরোটাই তুলে দিতাম… তবে ভরসা রাখতে পারেন, পাঠক – আমি সচেতন ছিলাম।
তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপিটা আমার হাতে তুলে দেবার মুহূর্তে তাঁকে যেভাবে খুব নিশ্চিন্ত মনে হয়েছিল, আমি চাই তিনি তাঁর লেখাটা সকলের সম্মুখে রাখতে পারায় সেভাবেই নিশ্চিন্ত হন।
আমরা কাহিনীটা শুনবো তাঁরই ভাষ্যে…
১
১৯৭১ সালের মার্চ মাস। তখন আমি ঢাকার কায়েদ-এ-আজম কলেজের (বর্তমান ‘সোহরাওয়ার্দি কলেজ’) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মে মাসে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা আসন্ন। তাই স্বভাবতই আমি আমার লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। এরই মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্সে ভাষণের ঘোষণা দিলেন। আমার বাবা মোহাম্মদ সিকন্দর আলী সাহেব তখন চিকিৎসার্থে ঢাকায় ছিলেন। ৭ মার্চে বাবা, বড় ভাই, মেঝো ভাই, আমি আর আমাদের এক মামাতো ভাই (ফারুক ভাই) যাই রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে। ঐ দিন সকাল থেকেই বিভিন্ন বয়সের লোকজন ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা হয়ে হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে মিছিল করতে করতে রেসকোর্স ময়দানে জড়ো হতে থাকেন। হাজার হাজার, লাখো লাখো জনতার ভীড়ে বঙ্গবন্ধু ভাষণ রাখলেন:
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বা-ধীনতার সংগ্রাম।
বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ শোনার পর মনে হতে থাকে – পরীক্ষা আর হবে না। সেখান থেকে ফেরার পথে বাবা সেই কথারই পুণরাবৃত্তি করলেন, আমার সাথে বাড়িতে চলে এসো, আমি বলছি, তোমাদের পরীক্ষা হবে না। আমার মনে হচ্ছে, দেশে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিন্তু এতদিন পরিশ্রম করে যে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলাম, তা হবে না- এমন কথা বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারলাম না। আর যদি সত্যিই পরীক্ষা, শেষ পর্যন্ত হয়েই যায়, তাহলে বিপদে পড়ে যাবো। বাবার ভবিষ্যদ্বাণীকে তাই গুরুত্ব দিলাম না।
বাবা পরদিনই আমাদের সিলেটের (শাহবাজপুর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার) গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে ‘সুরমা মেইল’-এ চড়ে রওয়ানা করলেন। তখন একটাই মেইল ট্রেন ছিল রাতের বেলা, রাত আটটা-সাড়ে আটটায় ঢাকা থেকে ছেড়ে পরদিন ভোরে সিলেটে পৌঁছাতো। বিদায় প্রাক্কালে বড় ভাই, মেঝো ভাই, আমি, আমার ছোটভাই আর মামাতো ভাই-ফারুক, সবাই কমলাপুর স্টেশনে গেলাম বাবাকে ট্রেনে তুলে দিতে। কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে ‘সুরমা মেইল’ ট্রেনটি দেখে তো আমরা অবাক। এতো লম্বা ট্রেন, অথচ পুরো ট্রেনে প্রায় ঠাশাঠাশি করে মানুষ- বিশেষ করে নারী আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তখন বাবা আমাদের বলেছিলেন, ট্রেনের অবস্থা দেখে বুঝে নাও, দেশের সামনে একটা সমূহ বিপদ আসন্ন। যাবার মুহূর্তে বাবা পরিবারের কর্তা হিসেবে বড় ভাইদেরকে আমাদের কথা বলে গেলেন, ওদের দিকে খেয়াল রেখো। খারাপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িতে চলে এসো। ট্রেন কমলাপুর ছাড়লে আমরা আমাদের ওয়ারীর বাসার দিকে চললাম। রাতে শুয়ে বাবার কথাগুলো বারবার মনে পড়তে লাগলো, আর সাথে মেইল ট্রেনের অবস্থাটাও চোখে ভাসতে থাকলো। পরের দিন মেঝো ভাইও ময়মনসিংহে তাঁর কর্মস্থলে চলে যান।
এর সপ্তাহখানেক পর বড় ভাইও বাড়িতে চলে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমার বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আমাদের একটা দোকান ছিলো (এখনও আছে) তৎকালীন জিন্নাহ এভিনিউতে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভিনিউ)। এই ব্যবসায়ের কারণে মামাতো ভাই-ফারুক, ফুফাতো ভাই-আফতাব আলী ভাইসহ সাত্তার নামে আমাদের এক সেলসম্যান আর বাবুর্চি খালেক ঢাকার ওয়ারীতে বাসা নিয়ে থাকতাম। সাথে আরোও ছিল আমার সহোদর ছোট ভাই – সাইকুল ইসলাম। বাসায় ৬ জনের সবাই পুরুষ, কোনো মেয়ে মানুষ থাকতেন না তখন। যা হোক, ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল খুবই কড়াকড়িভাবে। ফলে সবই অচল – লেখাপড়াও। তাই সময় কাটানোর জন্য দোকানে গিয়ে ভাইদের সহায়তা করাই শ্রেয় মনে করি।
২৫ মার্চ বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে হঠাৎ সব দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হতে থাকে। আমাদের দোকানও বন্ধ করে দেয়া হয়। দোকান থেকে বের হয়ে আমরা সবাই যখন ওয়ারীতে ফিরছি, তখন লোকজনের মাঝে কেমন একটা আতঙ্ক আতঙ্ক ভাব। ছোটখাটো পানের দোকানগুলোর রেডিও’র সামনে মানুষের জটলা। রাস্তা-ঘাটে বেরিকেড সৃষ্টি করা হচ্ছে। তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, একটা অশুভ সংকেত আমাদের দেশের জন্য অপেক্ষা করছে।
বাসায় পৌঁছে সবাই রেডিও শুনতে বসলাম। রেডিও শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। ভাবতে লাগলাম, এ অবস্থার ভবিষ্যৎ কী? রাতে খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরীক্ষার আশা আমি এখনও ছাড়িনি। সবাই ঘুমুতে গেলে আমি তখন বই-খাতা নিয়ে বসতাম, যেন একেবারে পড়ালেখা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ি।
রাত ১২টা বা সাড়ে ১২টার দিকে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলো। এবং সাথে সাথে প্রচন্ড শব্দে পুরো ঢাকা কেঁপে ওঠতে লাগলো। আমি এরকম গোলাগুলির শব্দ এর আগে জীবনেও শুনিনি, কী বিচিত্র আর ভয়ার্ত সে আওয়াজ! অন্ধকার ঢাকার আকাশে শুধু আগুনের ফুলকি। দূর থেকে মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিলো। আমি হতভম্ব। ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের জানালা দিয়ে ভাইদের ডেকে তুলে জানতে চাইলাম, ঢাকায় কী হয়েছে? এতো গোলাগুলি কিসের? সবাই বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে বসে থাকেন। আমাকেও বলেন মেঝেতে শুয়ে পড়তে। কেউই কিছুই বুঝতে পারছি না। আর এজন্যই হয়তো কেউই তখন আর স্বাভাবিক নই।
সেই ২৫ মার্চ রাত থেকেই আমরা ৬ জন গৃহবন্দী। এভাবে ২ দিন কাটলো। পুরো ঢাকা শহরে কারফিউ। ২৭ মার্চ সকালের দিকে কিছু সময়ের জন্য কারফিউ তুলে দেয়া হলো। আমরা সবাই বাসা থেকে বের হলাম। বাইরে বেরিয়ে গা শিউরে উঠলো। বাসা-বাড়ি, দোকানপাট সব জ্বলে ছারখার, রাস্তা-ঘাটে মানুষের লাশ আর লাশ, কাক আর কুকুর মানুষের লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে। নিজেকে স্বাভাবিক না রাখতে পেরে বাসায় ফিরে এলাম। মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়লাম সবাই। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ সবার। একমাত্র চিন্তা, কিভাবে এই শহর থেকে বের হওয়া যায়।
২৯ মার্চ সকালে কারফিউ তুলে দেয়া হলো। আমরা সবাই বের হয়ে পড়ি কমলাপুর স্টেশনের দিকে। রাস্তাঘাট জনশূণ্য, গাড়ি-রিকশা-শূণ্য। তাই আমরা ৬ জন পায়ে হেঁটে চলেছি। সবাই আলাদা আলাদা হয়ে হাঁটছি, কেননা তখন ঢাকাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ছিল যে, একসাথে ৩ জনের বেশি লোক চলাচল করতে দেখলেই গুলি করা হবে। আমরা যখন ফুটপাত ধরে হাঁটছি তখন এক লোক আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি। কমলাপুর স্টেশন যাচ্ছি শুনে ঐ ভদ্রলোক তখন আমাদেরকে উত্তেজিতভাবে বললেন, ঐ দিকে যাবেন না, পুরো কমলাপুর স্টেশন এলাকা পাক আর্মি ঘিরে রেখেছে। ওখানে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। তখনই উপলব্ধি করলাম, বিপদে পড়ে আমরা আমাদের হিতাহিত জ্ঞানও যেন হারিয়ে ফেলেছি। বুঝতেই পারছিনা কোন মৃত্যুকূপের দিকে চলছিলাম। নিরাশ হয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।
উত্তেজনায় আমরা যে আবার কখন গায়ে গায়ে মিশে গেছি, খেয়াল করিনি। তখন রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে পাক আর্মির একটা জীপ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিয়ে মতিঝিলের দিকে যাচ্ছিল। জীপের উপর একটা মেশিনগান তাক করা। সেখান থেকে একজন পাকিস্তানী সৈন্য জোরে ধমক দিলো, এ্যা, তুমলোগ এক এক কারকে যাও, ওর হামলোগ ফায়ার করদুংগা। আমরা আবার আলাদা আলাদা হয়ে চলতে লাগলাম। বাসায় পৌঁছে নিরাশায় আমাদের মনটা ভরে উঠলো।
এদিকে আরো নতুন নতুন দুশ্চিন্তা এসে গ্রাস করলো। যেখানে থাকতাম, তার আশেপাশে অনেক বিহারি থাকতো। তাই তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় করতে থাকলাম। আর যারা বাঙালী প্রতিবেশী ছিলেন, তারা যে কবে কখন কে কোথায় চলে গেছেন কেউ তার হদিস রাখেনি। নিরুপায় হয়ে আমরা ৬ জন লোক সেই বাসায় আরো দুই রাত কাটালাম। আমরা ইতোমধ্যে ধরেই নিয়েছি, আমাদের মৃত্যু যেকোনো সময় হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমরা তখনও বেঁচে ছিলাম।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা বারবার রেডিওতে ঘোষণা করছিল, যে যার কাজে যেন যোগদান করে। ৩১ মার্চ কারফিউ না থাকায় আমরা সকালে তাই দোকানের দিকে চললাম দোকানের অবস্থা কী, তা দেখতে। তখন নিজেদের কাজ, মানে দোকানদারী করার মতো পরিবেশ বা মানসিকতা থাকার প্রশ্নই উঠে না। গুলিস্তান সিনেমা হলের কাছে আসতেই দেখি একটা বাসকে ঘিরে বেশ জটলার সৃষ্টি হয়েছে। কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, বাসটা এখান থেকে যাবে টাঙ্গাইল। মনের ভেতরকার বাড়ি ফেরার সুপ্ত আশা আবার জেগে উঠলো। আমরা ৬টা টিকেট কেটে বাসায় ফিরলাম। আধাঘন্টা পরেই বাসটা ঢাকা ছাড়বে। বাসা থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ি আমরা। আফতাব আলী ভাইয়ের গায়ে শার্টের নিচে পেটের মধ্যে গামছা দিয়ে বেঁধে দোকানের ক্যাশের টাকা বাঁধা ছিল। আর শুধু মামাতো ভাই ফারুকের একটা চামড়ার ছোট স্যুটকেস ছিল, সে সেটা নিলো। তাতে তার ২/৪টা কাপড়চোপড় নিয়েছিল। কাপড়ের নিচে বঙ্গবন্ধুর একটা বিশাল ছবি আর ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটা লেখা একটা কাগজ ছিল (গানটা সুন্দর করে কোনো এক শিল্পীকে দিয়ে লিখিয়েছিল সে)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফারুক বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিল।
২
৩১ মার্চ সকাল ১১টার দিকে আমরা সেই বাসে করে টাঙ্গাইল রওয়ানা হই। আমরা মানে-আমি, আমার ছোট ভাই সাইকুল ইসলাম, মামাতো ভাই ফারুক, ফুফাতো ভাই আফতাব আলী ভাই, সেলসম্যান সাত্তার ও বাবুর্চি খালেক। বাসের ড্রাইভার ছিল বিহারি। বাস টাঙ্গাইল চললেও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ময়মনসিংহ। কেননা, আমার মেঝো ভাই নূরুল ইসলাম তখন ‘ফাইজার’ (বর্তমান নাম রেনিটা) ঔষধ কোম্পানীর হয়ে ময়মনসিংহ জেলার সেল্স ম্যানেজার হিসেবে কর্তব্যরত। তিনি সেখানেই থাকেন।
যাত্রা শুরু হলো। বাসে বসে সবাই অন্তর থেকে আল্লাহকে ডাকছি। কেননা, কোথায় পাক আর্মির মুখোমুখি হই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাসের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ ভদ্রলোক উঠেছেন। খুব সম্ভবত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ‘ইকবাল হলে’ থাকতেন। ২৫ মার্চ রাতে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। কিন্তু এই ৬/৭ দিন ধরে কোনো প্রাথমিক চিকিৎসা না পাওয়ায় গুলিবিদ্ধ স্থান থেকে পঁচা গন্ধ বের হচ্ছিল। পুরো বাসের যাত্রীদের সেই গন্ধে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু সবার মাঝেই এমন একটা মানসিকতা বিরাজ করছে যে, সেই গন্ধ নিয়ে কেউই তুলকালাম বাঁধিয়ে দিচ্ছেন না। সবার মানসিকতা যেন এককেন্দ্রিক – সবাই নিজেকে নিয়ে মগ্ন; সবাই আত্মকেন্দ্রীকতায় বিভোর।
পথিমধ্যে এক স্থানে একটা দীর্ঘ ব্রিজের উপর পাক আর্মি আমাদের পথরোধ করলো। তারা বালুর বস্তা দিয়ে শেল্টার নিয়ে সেখানে মেশিনগান তাক করে বসেছিল। দায়িত্বরত এক পাক আর্মি উর্দুতে জানতে চাইলো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে। উর্দুভাষী বিহারি ড্রাইভার জানালো, বাসের সব যাত্রী সরকারি কর্মচারী, অফিস টাঙ্গাইলে। তাই সবাই টাঙ্গাইলযাত্রী। বাঁচানোর মালিক আল্লাহ, সে যাত্রায় আমাদের ছেড়ে দেয়া হলো।
অনেকদূর যাবার পর অনেকটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আবার পাক আর্মিরা আমাদের পথরোধ করলো। স্থানটা অতোটা মনে পড়ছে না, সম্ভবত [যদ্দুর মনে পড়ে] জয়দেবপুরের কাছাকাছি কোনো স্থানে। এবারে সবাইকে সাথের সবকিছু নিয়ে বাস থেকে নেমে দাঁড়াতে বলা হলো। বাসের সবাইকে নিয়ে পাশের জঙ্গলের সামনে লাইন করিয়ে হাত উঁচু করে দাঁড় করানো হলো। যার যা কিছু ছিল, সামনে রাখতে বলা হলো। সবাই মনে মনে কলেমা পড়তে (আল্লাহকে স্মরণ) থাকি। সবার শরীর আর জিনিসপত্র চেক করতে লাগলো হানাদাররা। আমাদের বুক ঢিব ঢিব করছে ফারুকের ব্যাগটার জন্য। যদি ঐ ব্যাগে বঙ্গবন্ধুর ছবি পায় ওরা, তাহলে এখানেই সবার সমাধি হয়ে যাবে। কিন্তু রাখে আল্লাহ, মারে কে – ব্যাগের উপরকার কাপড়চোপড়ে আঙ্গুল চালিয়ে যেন ওরা অস্ত্র বা গ্রেনেড খুঁজলো। বেঁচে গেলাম আবারো।
আবার শুরু হওয়া সেই বাস যাত্রা কিছুদূর যেতেই থমকে দাঁড়ালো। কারণ সামনের ব্রিজটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাধ্য হয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম। নিচের নদী শুঁকিয়ে আছে, তাই ব্রিজের নিচ দিয়ে হেঁটে ওপারে গিয়ে ওঠলাম আমরা। এবারে পায়ে হেঁটে চললাম সামনের দিকে; উদ্দেশ্য সামনে কোনো বাজার যদি পাওয়া যায়…।
কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখি কয়েকটা জীপ আমাদের সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। যে যেদিকে পারলাম, ছুটলাম। আমরা পাশের একটা খালে গিয়ে কাদা-পানির মধ্যে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণ গেলে সবার ভেদ ভাঙলো – এরা পাক আর্মি নয়, আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে এই সকল এলাকা দখল করেছে। এঁদের এখানে দেখে মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম; যাক, পাক আর্মিরা সহসাই এখানে আসতে পারবে না, আসতে হলে একটা যুদ্ধ করে তবেই আসতে হবে।
ওখানকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা সত্যিকার অর্থেই তাঁদের সাধ্যমতো অর্থকড়ি আর যানবাহন দিয়ে আন্তরিকভাবে সহায়তা করছিলেন ঢাকা আর চট্টগ্রাম থেকে আসা বিপদগ্রস্থ লোকদের। এই উদ্বাস্তুদের আওয়ামী লীগ কর্মীরা ট্রাক-বাস দিয়ে সামনেই মধুপুরে নিয়ে গেলেন। সেই দলে আমিসহ আমাদের ৬ জনের দলটা ছিল। মধুপুরে একটা বিশাল ঘরে আমাদের বিশ্রাম আর খাবার ব্যবস্থা করলেন তারা। সবাইকে খাবার হিসেবে মুড়ি, গুড় আর পানি দেয়া হলো। যে ঘরটাতে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো, সেটা হিন্দু বাড়ির একটা পূঁজার ঘর।
তখন প্রচন্ড শীতের রাত। তাছাড়া গ্রামে সেই শীত যেন আরো জেঁকে বসেছে। মেঝেতে একখানা তেরপল বিছিয়ে দেয়া হলে আমরা তাতেই শুয়ে পড়ি। সবার মনের মধ্যেই ভয় আর আতঙ্ক। আমার গায়ে একটা শার্ট আর প্যান্ট। তাই শীতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। বিপদ বোধহয় মানুষের সহ্য ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। আমরা ওই শীতের মাঝেই সেখানে গুঁটিশুঁটি হয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।
এপ্রিলের ১ তারিখ। অথচ তখন দিন-তারিখের কোনো খেয়ালই ছিল না। ভোরে ৪/৫টা ট্রাক এসে আমাদের সবাইকে তুলে নিল। ট্রাকগুলোতে ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঠাশা ছিল। বেলা ১০টার দিকে ট্রাকগুলো আমাদের সব আরোহীকে ময়মনসিংহ পৌঁছে দিল। ময়মনসিংহ শহরে পৌঁছে দেখি, পুরো শহরেই বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। বুঝতে পারলাম, এখনও হানাদাররা এখানে পৌঁছায়নি। আমরা তিনটা রিকশা নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের সামনেই মেঝো ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম। মেঝো ভাই আমাদের নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আমরা প্রথম রাতেই মারা গেছি। কারণ এরপর পুরো এক সপ্তাহ আর কোনো যোগাযোগই ছিল না উভয়পক্ষের মধ্যে। আমাদেরকে তাই জীবন্ত অবস্থায় সামনে দেখে মেঝো ভাই যার-পর-নাই খুশি হয়েছিলেন। তিনি ওখানকার বাড়িওয়ালাকেও খবর দিলেন। বাড়িওয়ালা এসে আমাদের দেখে যেন হাফ ছাড়লেন, সবার জন্য দোয়া করলেন।
মেঝো ভাই ঢাকার বাবুর্চি খালেককে নিয়ে তক্ষুণি কাঁচাবাজারে গেলেন। বাজারে তখন মুরগী খুব সস্তা ছিল। মেঝো ভাই আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ শার্ট, জামা, লুঙ্গি পরার জন্য দিলেন। কেননা ঢাকা থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বাজার করে এনে খালেককে রান্না চড়াতে বলে দিলেন। খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। এভাবে প্রায় ১৫/২০ দিন ময়মনসিংহ থাকলাম আমরা।
এরই মাঝে একদিন শোনা গেলো ময়মনসিংহ পাক আর্মি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। মেঝো ভাইয়ের বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক টিএন্ডটি’র ইঞ্জিনিয়ার। তাই ওনার কাছ থেকে প্রায়ই ঢাকার সংবাদ পাওয়া যেত। হঠাৎ একদিন তিনি অফিস থেকে এসে জানালেন, আজ রাতে পাক আর্মি ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করবে। সেদিন পুরোটা দিন জুড়েই একটা জঙ্গি বিমান আকাশে টহল দিচ্ছিল। বাড়িওয়ালা সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে ময়মনসিংহ শহরের বাইরে প্রায় ১৫/২০ কিলোমিটার দূরে তাঁর বড় ছেলের শ্বশুড়বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ নিয়ে তুললেন। অপরিচিত-পরিচিতের সূক্ষ্ম হিসাব তখন নিতান্তই একটা খসড়া হিসাব, জীবন-খাতায় সেই হিসাব তখন একেবারেই বেমানান। মানুষ হলেই মানুষের সহায়তা করছে। আর মানুষ হয়েও পাক আর্মি মানুষ মারছে। জীবন ঘড়ির কাটাই যেন উল্টা চলছে।
ঈশ্বরগঞ্জের সেই বাড়িতে আমরা দুই-তিনদিন থাকলাম। সেখানেও মানুষজন আতঙ্কে। আমাদের আফতাব আলী ভাইকে নিয়ে পার্শ্ববর্তি বাজারে গেলে তার লম্বা-চওড়া দেহ কাঠামো দেখে লোকজন আতঙ্কে তাঁকে বিহারি সন্দেহ করে বসতেন। সে যাহোক, ওখানে থেকে-থেকেই খবর পেলাম, পাক আর্মি কোনো অবস্থাতেই ময়মনসিংহ শহরে ঢুকতে পারছে না। তাই আমরা ঈশ্বরগঞ্জ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এলাম ময়মনসিংহে, মেঝো ভাইয়ের বাসায়।
এর দুই তিনদিন পর মামাতো ভাই ফারুক আর ফুফাতো ভাই আফতাব আলী ভাই মেঝো ভাইয়ের কাছে প্রস্তাব করলেন সবাই বাড়ির পথে রওয়ানা হবার জন্য, কারণ তাঁরা মনে করছেন এই যুদ্ধ কোনো অবস্থাতেই থামবে না। মেঝো ভাই রাজি না হওয়াতে বাকিদের রেখে তাঁরা দুজনই বাড়ির পথে রওয়ানা দেবার প্রস্তাব দিলেন। মেঝো ভাই বিচক্ষণ মানুষ, এই চরম বিপদের মাঝেও মাথা ঠান্ডা রেখে ভেবেচিন্তে দেখলেন এই চরম বিপদে দুজন মানুষকে একা বাড়ির পথে ছেড়ে দিয়ে যদি পথে তাদের কোনো বিপদ হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত বড় ভাই হিসেবে তাঁকেই দোষী হতে হবে। তাই তিনি একটা কাগজে দুজনের বন্ড সই নিয়ে বাড়ির পথ ধরতে অনুমতি দিলেন। পরদিন ফযরের নামায পড়েই তাঁরা দুজন বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদেরকে আমাদের থেকে চলে যেতে দিয়ে আমরা খুব একা হয়ে পড়লাম।
৩
এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল এর মধ্যেই। হঠাৎ একদিন দুপুরে মেঝো ভাইয়ের অফিসের বস্ আলী হোসেন সাহেবের কাছ থেকে খবর পেয়ে মেঝো ভাই বাসায় এসে আমাকে আর আমার ছোট ভাইকে বললেন, আজ সন্ধ্যার আগেই আমাদের ময়মনসিংহ ছেড়ে চলে যেতে হবে, নতুবা প্রাণ হারাতে হবে। এরকম হুটহাট দুঃসংবাদ যদিও আগে শুনেছি, কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমাদের দুজনের প্রচন্ড ভয় লাগতে থাকে। দেরি না করে তখনই একান্ত জরুরি কিছু জিনিসপত্র আর শীত ঠেকাতে গরম কাপড় একটা কালো স্যুটকেসে ভরে রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা ৫ জন – আমি, ছোট ভাই, মেঝো ভাই, সাত্তার আর খালেক। বাবুর্চি খালেকের মাথায় স্যুটকেস। আমাদের উদ্দেশ্য যদিও বাড়ি পৌঁছা, কিন্তু যে বিপদসংকুল পথে যাত্রা করছি তাতে এক মুহূর্তেরও জীবনের গ্যারান্টি নাই। তাই আমরা যেন অজানার পথেই যাত্রা করলাম।
শহরে বেরিয়ে দেখি শহরে যেন মানুষজন নেই। রাস্তা ধরে আমরা যখন দুরু দুরু বুকে হাঁটছি, তখন দেখি স্থানীয় বাঙালি যুবকদের হাতে ডেগার, তলোয়ার, রাম দা। সেই সব রাম দা থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। মনে হলো এইমাত্র কাউকে জবাই করা হয়েছে ওই রাম দা দিয়ে। তাদেরই একজন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে জানতে চাইলো আমরা বিহারি না বাঙালি। আমরা সবাই বললাম, বাঙালি ..বাঙালি। ‘বাঙালি’ শুনেই তারা আমাদের দ্রুত শহর ছাড়তে বললো; আবার এটাও জানিয়ে দিল, নাহলে মৃত্যু অনিবার্য। আমরা দ্রুত পায়ে হেঁটে নিকটবর্তী নদী পার হতে নদীর পাড়ে উপস্থিত হলাম। কারোরই বুঝতে বাকি থাকলো না যে, এই সব যুবকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিহারিদের খুন করছে। নৌকা করে নদী পার হয়ে ওপাড়ে গিয়ে পরম সৌভাগ্যবশত তিনটে রিকশা নিলাম। উদ্দেশ্য – নেত্রকোনা। কিন্তু এই বিপদের কারণেই হয়তো রিকশা ভাড়াও বেড়ে গেছে। মাত্র ২ কিলোমিটার রাস্তার ভাড়াও তখন ৳৬০ [টাকা]। তখনকার দিনে ৳৬০ [টাকা] রিকশা ভাড়া শুনেও আমরা রাজি হয়েছিলাম; কারণ, তখন জীবন বাঁচানোর এক প্রচন্ড খেলায় মত্ত আমরা।
আল্লাহ আমাদের সহায় ছিলেন। চাকরিসূত্রে নেত্রকোনার প্রায় জায়গাই মেঝো ভাইয়ের পরিচিত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সাথেও সুসম্পর্ক ছিল। মেঝো ভাই রাত ১০টার দিকে নেত্রকোনা শহরের একটি ফার্মেসির সামনে থামলেন। ফার্মেসির মালিকের সাথে দেখা হতেই ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যা ভাষায় বোঝানো মুশকিল। তিনি পাশেই তাঁর বিরাট বাড়িতে নিয়ে গেলেন আমাদের। রাতের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, আমাদের আরাম আয়েশের সুব্যবস্থা করে থাকার ব্যবস্থাও করে দিলেন। পরদিন খুব ভোরে নাস্তা করিয়ে সেখানে থেকে কিভাবে কোন পথে যাবো, তার সব পথ বাতলে দিলেন। আমরা সেই নির্দেশনায়ই পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়ে গেলাম মোহনগঞ্জ শহরের দিকে।
দেশের এই চরম দুর্দশায় রিকশা, গাড়ি সব বন্ধ হয়ে গেছে; শুধু দুয়েকটা গরুর গাড়ি ছিল। কিন্তু এতো এতো উদ্বাস্তুর জন্য মুষ্টিমেয় গরুর গাড়ি নিতান্তই যৎসামান্য। তাই লোকজন প্রাণ বাঁচাতে পায়ে হেঁটেই চলছেন যে যার গন্তব্যে; মাইলের পর মাইল। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-জোয়ান সবারই একই অবস্থা। আমরা পায়ে হেঁটে মোহনগঞ্জ বাজারে পৌঁছলাম দুপুর আড়াইটা/তিনটার দিকে। সেখানেও আল্লাহর দয়ায় মেঝো ভাইয়ের পরিচিত আরেক ঔষধ ব্যবসায়ী আমাদের সহায়তা করেন। ঔষধ ব্যবসায়ী হিন্দু ভদ্রলোক (ডাক্তার ছিলেন কিনা মনে নেই) – আমাদেরকে এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করালেন। তিনি আমাদের একটা ভালো উপদেশ দিলেন। মেঝো ভাইকে বললেন, ইসলাম ভাই, সবই তো ফেলে এসেছেন। এবারে আপনাদের পায়ের চামড়ার জুতোগুলো বাদ দিয়ে সবাই কাপড়ের জুতো কিনে পরেন। কেননা, আপনাদেরকে এই মোহনগঞ্জ থেকে আরো দশ বারো দিনের ‘হাঁটা পথ’ পাড়ি দিতে হবে। ভদ্রলোকের কথার সত্যতা উপলব্ধি করে তখনই আমরা একটা দোকানে গিয়ে সাদা কাপড়ের জুতো কিনে নিই। ডাক্তার সাহেব আমাদেরকে রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন বাজারেরই একটা খালি হয়ে পড়া দোকান ঘরে। পরদিনই চামড়ার জুতোগুলো ঐ দোকান ঘরে রেখে পায়ে কাপড়ের জুতো পরে রওয়ানা করলাম নতুন করে।
এবারের যাত্রা শুরু হলো আরো বন্ধুর পথে। যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। তাই হাওড়ের মধ্য দিয়ে, ধানের জমির মধ্য দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে চলেছি। বাবুর্চি খালেকের মাথায় এর মাঝে আবার আমাদের সেই কালো স্যুটকেস। যাত্রার ক্লান্তি আর বিষণ্নতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি আমরা। কেননা আমাদের ‘গন্তব্য’ থাকলেও গন্তব্যে পৌঁছার অনিশ্চয়তা আমাদেরকে হতাশায় ডুবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মানুষ বলেই হয়তো হতাশাকে চাপা দিয়ে আমরা সেই অনিশ্চিত সম্মুখ পথে চলছিলাম। হাঁটা পথে সন্ধ্যা নামলে কোনো বাজার কিংবা নদীর কোনো ভাসমান নৌকায় আশ্রয় নিতাম। ভোর হলেই আবার আমরা বেরিয়ে পড়তাম। এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে একদিন ছাতকের ধিরাই বাজারে গিয়ে একটা ডিঙি নৌকা পেলাম। হাঁটা পথের বিকল্প হিসাবে ওই ডিঙির মাঝির সাথে কথা হলো, মাঝি আমাদের কথায় রাজি হলেন। না, গন্তব্য পর্যন্ত নয়; যতটুকু পারা যায়, ততটুকু পর্যন্ত অগ্রসর হবার চুক্তি হলো আমাদের মধ্যে। শুরু হলো আমাদের ভাসমান জল-জীবন।
নৌকায় আরোহী আমরা ৯ জন। আমরা পাঁচজন ছাড়াও নৌকায় বয়স্ক মাঝি আর তার ছেলে মিলে দুজন। এছাড়াও আমাদের সাথে ইতোমধ্যে নতুন দুজন যাত্রাসঙ্গী জুড়েছেন। এক ভদ্রলোক মোহনগঞ্জ থেকে উঠেছেন, যাবেন ফেঞ্চুগঞ্জে। তিনি আমাদের বড় ভাইয়ের বয়সী আর বেশ অমায়িকও; তিনি ময়মনসিংহে সরকারি চাকরি করতেন। অন্যজন কুলাউড়া জংশনের স্টেশন মাস্টার; উনি বেশ বয়স্ক ছিলেন। আমরা নৌকায়ই আমাদের ভ্রাম্যমান সংসার পাতি। নদীর কোনো মাছধরা নৌকা থেকে মাছ কেনা হতো, মাঝি আর তার ছেলে সেগুলো রান্না করতেন। নৌকা দিনের বেলা অবিরাম চলতে থাকতো; রাতে আমরা কোথাও নৌকা ভিড়িয়ে বিশ্রাম নিতাম।
এভাবেই চার-পাঁচদিন চলার পর আমরা এক রাত্রে ফেঞ্চুগঞ্জের নদীর কোনো একটা ঘাটে পৌঁছলাম। এখানে, আমাদের পথসঙ্গী দুজন আমাদের থেকে বিদায় নিলেন। বিপদের বন্ধুই যে প্রকৃত বন্ধু, তার প্রমাণ পেলাম বিদায়কালে তাঁদের চোখে পানি দেখে। তাঁরা তাঁদের সাথে তাঁদের বাড়িতে আমাদেরও যেতে বললেন, কিন্তু তখন সময়ের অভাব আর দেশের অরাজকতায় নিজের বাড়িই বেশি আকাঙ্ক্ষিত, তাই তাঁদের অনুরোধ আমরা রাখতে পারিনি।
আমাদের ৫ জনকে নিয়ে নৌকা আবার চলতে শুরু করলো। ফেঞ্চুগঞ্জের ঐ ঘাট থেকে একটু অগ্রসর হয়ে হাওড়ের মধ্যে এসে বুড়ো মাঝি নৌকা ভিড়ালেন। রাতের আঁধারে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সেদিনকার জন্য সম্ভব নয়। নৌকায় একটা হারিকেন জ্বলছে, তার আলো কমিয়ে দিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। দূরে কোথাও মর্টার শেলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কায় আরেকটি রাত পার করলাম।
ভোরে মাঝি চাচা আবার নৌকা নিয়ে চললেন। সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটার দিকে আমরা মৌলভীবাজারের এলাকার নদীর কোনো ঘাটে আসি। নিজেদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে সবাই নৌকা থেকে নামলাম। উদ্দেশ্য, সামনের বাজারে গিয়ে খাবারের খোঁজ করা। আমরা যেই নৌকা থেকে নেমে বাজারের দিকে অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে কোনো এক বাঙালি সৈনিক (সম্ভবত মুক্তিবাহিনীর) এসে আমাদেরকে শাসালো, তাঁর বক্তব্যে রূঢ়তা, আমরা কেন ওখানে উঠলাম? সৈনিক আমাদেরকে দ্রুত নৌকায় ফিরে যেতে বললো আর ওখান থেকে সরে পড়ার জন্য আদেশ করলো। বিপদের আভাস পেয়েই কিনা জানিনা আমরাও পড়িমড়ি করে নৌকায় উঠে নৌকা ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম না, কেনোইবা সে আমাদেরকে এভাবে তাড়িয়ে দিলো। কিন্তু বিপদ দেখেই যে এমনটা করেছে, তা বুঝেছি সবাই-ই। …আমরা নৌকায় করে পালাচ্ছি।
আল্লাহর কী অশেষ কৃপা, আমরা নৌকা ছাড়তেই পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই দুটো পাকিস্তানি মিগ-ফাইটার এসে মৌলভীবাজার শহরের আশেপাশের গ্রামে হামলে পড়ে। মিগ দুটো মারাত্মকভাবে বোমাবর্ষণ আর বৃষ্টির মতো মেশিনগানের গুলি চালাতে থাকে। চোখের সামনেই বাজার উড়ে গেলো; দাউ দাউ করে জ্বললো আগুন। কতো শিশু-নারী-পুরুষ মারা পড়লেন মিগের মেশিনগানের ছররায় আমাদেরই চোখের সামনে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ওই বাজারেই খাবার জন্য আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম; সৈনিকের কথা না শুনলে হয়তো এই খাওয়াই জীবনের শেষ খাওয়া হতো। কেনো জানি ভাবতে ইচ্ছে করে, ঐ সৈনিক একজন ফেরেশতা ছিলেন, আমাদের জীবনে আরো কিছু মুহূর্ত যোগ করার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
মিগ দুটো বারবার আমাদের নৌকার খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ভয় হলো, মেশিনগানের গুলি না নৌকায় পড়ে নৌকাও ঝাঁঝরা করে দেয়। মাঝি চাচা তাই দ্রুত নৌকাটাকে নদীর উপর হেলে পড়া একটা গাছের নিচে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। মৃত্যুর প্রহর গুনছি আমরা, আর মনে মনে কলেমা জপে চলেছি। সবার কী কান্নাকাটি, আর আল্লাহর কাছে প্রাণভিক্ষা! যেকোনো মুহূর্তে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আমাদের তিনভাইয়ের সলিল সমাধি হতে পারে। মরলেও যেন একসাথে থাকতে পারি, তাই পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে বসে আছি। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই বাঁচাতে পারে।
প্রায় আধাঘন্টা ধরে এই তান্ডব লীলা আর মৃত্যুর তিক্ত স্বাদের কাছাকাছি থেকে জানলাম, জীবন-মৃত্যুর কাছাকাছি থাকার স্বাদ যে কতো তিক্ত। হয়তো সেই তান্ডব দেখার জন্যই আমরা বেঁচে থাকি। এ যাত্রায় মৃত্যুর এতো কাছাকাছি থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা যেন নতুন জীবন পেলাম; কেন জানি মনে হলো, আল্লাহ আমাদেরকে এই যুদ্ধে আর মারবেন না; দিব্য-দয়ায় বাঁচিয়ে রাখবেন নিশ্চয়ই। ঐ দিনই বিকেল ৫টার দিকে আমরা গন্তব্যস্থানের কাছেই একটা নদীঘাটে পৌঁছাই। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মাঝি চাচাকে যথোচিত অর্থকড়ি দিয়ে আমরা তাঁর থেকে বিদায় নিলাম; চাচাকে বললাম, আমাদের জন্য দোয়া করতে। ঐ সময় বোধহয় কাউকে বলা লাগেনা, সবাই এমনিতেই সবার জন্য দোয়া করে চলেছে।
মাঝি চাচার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করি। এভাবে আমরা তিনভাই আর প্রভুভক্ত বাবুর্চি খালেক নিরাপদেই পৌঁছে যাই বড়লেখায় আমাদের বাড়িতে। খালেকের বাড়ি অবশ্য ছিল কুমিল্লায়, কিন্তু সে তাঁর মা-বাবাকে বাধ্য হয়ে দূরে রেখেই আমাদের বাড়িতে থেকে গেলো। আমরা পৌঁছি ঠিকই, কিন্তু কী বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, তা শুধু আমরা বুঝবো আর আল্লাহই বুঝবেন। তবে, আমরা হয়তো পৌঁছতে পেরেছি; হয়তো এমনও মায়ের ছেলেরা আছে, যারা পারেনি জন্মদাত্রি মায়ের কোলে ফিরে যেতে; বরং পথেই তাদের জন্মভূমিতে সমাধি হয়ে গেছে। তাঁদের দিকে তাকিয়েই চলার ক্লান্তি ভুলে যাই।
__________________________________
বর্ণনাকারী আমার সেজ মামা সাইফুল ইসলাম; বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী। মেঝো মামা নূরুল ইসলাম আর চতুর্থ মামা সাইকুল ইসলাম আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন আজীবনের জন্য (আল্লাহ তাঁদের আত্মার শান্তি দিন)। মেঝো মামা জীবিত থাকাকালীন আমি মামা’র লেখা যথাসম্ভব যাচাই করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।
প্রচ্ছদের ছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে নেয়া^। মূল প্রস্তুতকারক: Himasaram।